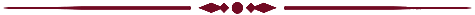
বিজোড় সংখ্যার মাত্রার পর যতি ব্যবহার করেছেন মধুসূদন তাঁর মিশ্রকলাবৃত্তে এই ছন্দের চলতি নিয়ম ডিঙিয়ে, অনেকের কাছেই সেটা বেশ অস্বস্তির কারণ ছিল। এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ 'প্রথম দরজা' প্রবন্ধটিতে জানিয়েছেন যে বিজোড় সংখ্যার মাত্রার পর প্রয়োজনমতো যতি-পতন আনার সাহস দেখিয়েছিলেন বলেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মধ্যে একটা সামর্থের স্বর তৈরি হয়..." এই রীতিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন বলে মধুসূদন তাঁর ছন্দে আনতে পেরেছিলেন পৌরুষ ছন্দের পৌরুষ! এটুকু পড়েই মধুসূদনের হাতে গড়া ছন্দটিকে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাই যেন। রাবণের অনমনীয় মাথার উপর মুকুট হয়ে জ্বলতে থাকে সেই মিশ্রকলাবৃত্ত। ইন্দ্রজিতের প্রয়াস আর পরাভবের মাঝখানে এক অপ্রতিহত দ্যুতি ছড়ায় যেন মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর।

কিন্তু শুধু ছন্দই নয়, গোটা কাব্যটিই আসলে উনিশ শতকের অপ্রতিহত পৌরুষের ভাষ্য। আর সেই 'পৌরুষ', অথবা শৌর্য-পরাক্রম-পুরুষকার, যেভাবেই চিহ্নিত করি তাকে, ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সেটি প্রচলিত এবং মান্য কতগুলি নির্দিষ্ট ধারণা-পোষিত শব্দ হয়ে ওঠে, যা আসলে সমাজের লিঙ্গ-ভিত্তিক ধারণাকে প্রকাশ করে। বস্তুত এটা বলা যায় যে, সমাজ-চলতি একটি পুংজেন্ডার-ভাবনা মধুসূদনের এই কাব্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।
মধুসূদনের রাবণ আমাদের গভীর মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই যে রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন নিজেই রাবণ প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন যে, ওই চরিত্রটি তাঁর কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং রাবণকে চমৎকার মানুষ বলেই মনে করেন তিনি, - অতঃপর আমরাও মূলত তাঁর নির্দেশিত পথেই তাঁর রাবণের মূল্যায়ন করেছি এবং চরিত্রটির অপরাজেয় পৌরুষের আদর্শ আর তার শোচনীয় পরাজয়ের বাস্তবতা, এই দুইয়ের প্রেক্ষিত মনে রেখে তার নিয়তিতাড়িত পরাভবকে, অনুভব করে, চরিত্রটির সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে নিজেদের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেছি। ষষ্ঠ সর্গে, মেঘনাদের মৃত্যু দৃশ্যটি শুধু কবিকেই কাঁদায়নি, "লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।/ নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি/ শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে" - এই মৃত্যুদৃশ্যের বিষাদ যেকোনো পাঠকের মনকেই সজল করে তোলে। নবম সর্গে নিজের সমস্ত স্বপ্নের ভস্মপরিণামের সামনে রাজ্যজোড়া চিতাগ্নির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, যে রাবণ জীবনের শূন্য পরিনাম প্রত্যক্ষ করেন, তার দিগন্তবিস্তৃত শোক আমাদের আচ্ছন্ন করে নিশ্চয়ই; কিন্তু এই শোক আমরা বয়ে নিয়ে চলি তা দুর্বলের নয়, বীরের শোক বলেই।
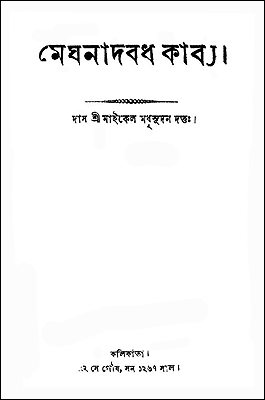
বীররসের প্রতি একটি পক্ষপাত নিয়ে 'মেঘনাদবধ' লিখতে শুরু করেছিলেন কবি। বীররসের প্রতি এক ধরনের ঝোঁক বাংলাদেশের উনিশ শতকের চরিত্রের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। জড়তা ও সংস্কারের প্রভাবমুক্ত এক নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের আলোয় উনিশ শতকে যখন বাঙালি তার নিজস্ব একটি জাতীয় চরিত্র গঠনের সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু করেছিল, সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের জন্য এই সময়ের কবিতা অনেক সময়ই মহাকাব্য-প্রকরণটিকে উপযুক্ত মনে করল, - তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক বাংলা কাব্য' বইটির এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গত মনে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মেঘনাদবধ-এ কোন রস-পর্যায়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে, বীর অথবা করুণ, এই চেনা তর্ক দূরে সরিয়ে রাখলেও একথা সাধারণভাবে বলা যায়, বাংলা কবিতায় সমগ্র উনিশ শতকে বীররসের প্রতি একটা সমর্থন লক্ষ্য করি আর এই ঝোঁকই উনিশ শতকের বাংলা মহাকাব্য-প্রতিম রচনাগুলিকে একটি সমাজগ্রাহ্য চেনা ছাঁদের ম্যাসকুইলিনিটি বা পুরুষালি স্বভাবে নিষিক্ত করে রাখে।
মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, এই দুটি চরিত্রের দীপ্তির কথা আমাদের শৈশবে প্রায়ই আলোচিত হতো। "জানি স্নেহে সে নারী, জানি বীর্যে সে পুরুষ" চিত্রাঙ্গদার এই পরিচয়ে মুগ্ধ হতে গিয়েও আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, অন্তত একবার নয়নলোভন নারীত্ব তাকে অর্জন করতেই হলো অর্জুনকে পাওয়ার জন্য। স্নেহশীলতাকে নারীধর্ম আর বীরত্বকে পুরুষস্বভাব বলে দেগে দেওয়ার মধ্যেও সমাজপোষিত চেনা মুদ্রাই খুঁজে পাই। রবীন্দ্রনাথের আগেই, কমনীয়তা ও লাস্য এবং শৌর্যকে কোনওভাবে যেন মিলিয়ে নেবার কথা ভেবেছিলেন মধুসূদন প্রমীলা চরিত্রটির উপস্থাপনায় "অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে/ আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?" মনোহারিণী প্রেয়সী আর শক্তিময়ী বলদাত্রী হয়ে ওঠার মধ্যে যে কোনো বিরোধ নেই, এটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল এখানে। যোদ্ধাবেশে ইন্দ্রজিতের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুকে পরাস্ত করবে, রাঘব বংশকে ধ্বংস করবে, 'নতুবা মরিব রণে', প্রমীলার এই প্রতিজ্ঞায় আমাদের তাকে যথার্থ বীরাঙ্গনা বলেই মনে হয় প্রায়। বিদ্যুৎগতিতে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সখীদের কাছে সংগ্রামের এমন পরিকল্পনার কথাও সে জানিয়েছে। তখন সে মত্ত-মাতঙ্গিনী, অথবা যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।
সালংকারা সিঁদূর-চর্চিতা বিষাদময়ী প্রমীলা সেখানে 'মর্তে রতি, মৃত কাম সহ সহগামী'। অতএব এটা বোঝা কঠিন নয় যে বীররসের যে কাব্যটি লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন মধুসূদন, তা মূলত কাব্যের মূল পুরুষ-চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। পুরুষস্বরই এ কাব্যে মুখ্য। প্রমীলা বা তার কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ সখী, যাদের এ কাব্যে কখনও কখনও বীরাঙ্গনা বলা হয়েছে, রণসাজে সজ্জিত মুহূর্তেও তারা পুরুষের দৃষ্টি-শোভন। তৃতীয় সর্গে তারা যখন শত শঙ্খে রণঘোষণা করেছে, সম্মিলিতভাবে ধনুকে টঙ্কার দিয়েছে, তখন কবির বর্ণনা অনুযায়ী 'কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে'; অশ্বে-হাতিতে আরূঢ় যোদ্ধারা কেঁপে উঠলেন। সিংহাসনে রাজা, অবরোধে কুলবধূ, কুলায় পাখিরা, পর্বতগহ্বরে সিংহ, বনে বনহস্তী সকলেই সন্ত্রস্ত হলো। এই ত্রাসসঞ্চারের বিবরণে উৎসাহিত পাঠকের মনে প্রমীলাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্রিয়া দেখার বাসনা হলে, শেষপর্যন্ত তাকে নিরাশ হতে হয়। হনুমানের পাহারা পার হয়ে রামের কাছে পৌঁছে দূতী জানিয়েছিল তাদের বাসনা, "আসি যুদ্ধ করো তাঁর সাথে;/ নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী/ স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।" অথবা সে জানিয়েছে 'রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে, বীরেন্দ্র'। একাকিনী যে কোনও রাক্ষসকন্যাই রামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অসিযুদ্ধে সক্ষম, একথা জানিয়ে যুদ্ধবাসনায় অধীর হয়েছে সে 'যথারুচি কর দেব, বিলম্ব না সহে।'
তবু সেই পারদর্শিতা একটি বিবৃতি বা স্টেটমেন্ট হয়েই থেকে গেল, সেই পারঙ্গমতার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাব্যে হাজির করার তাগিদ অনুভব করেননি কবি। বরং এক্ষেত্রে প্রমীলাসহ লঙ্কাপুরীর দানব-নন্দিনীদের ওই যুদ্ধ-বাসনাকে নিবৃত্ত করেছে রামের সৌজন্যবোধ ও শিভ্যালরি। নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না সে, নারী-পুরুষের যুদ্ধ অসম বলেই, হয়তো একথা সরাসরি না জানিয়ে সৌজন্য রক্ষা করে তিনি জানিয়েছেন যে, অকারণে কোন তুচ্ছ হেতু নিয়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন না তিনি - 'বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে'। বিশেষত স্বর্ণলঙ্কার 'কুলবধূ' 'কুলবালা'দের প্রতি কোনও বৈরীভাব পোষণ করেন না তিনি। প্রমীলার দূতীর কাছেই প্রমীলার পতিভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে রাম জানালেন, "কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি ললনে,/ তাঁর পতিভক্তি আমি,.../ বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।" আমাদের অভ্যস্ত সমাজ কাঠামো যেন রামের এই সৌজন্য প্রকাশে স্বস্তি পেয়ে যায়।
প্রমীলা তার রাজ্যের নিভৃত পরিসরে বীরাঙ্গনা হতে পারে, অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে, তার প্রিয় সখীরা সকলেই হয়তো প্রশিক্ষিত যোদ্ধা, তবুও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ যে পাওয়ার স্ট্রাকচারের বিন্যাস আছে, সেখানে নারী দৃশ্যত অ্যাক্টিভ হয়েও আসলে প্যাসিভ। অন্তত পুরুষে-পুরুষে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার জয়-পরাজয় নির্ণয়ে নারী কখনও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতেই পারেনা। এমনকি পুরুষের সেই সংগ্রামের পরিসরের মধ্যে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যদিও এই কাব্য প্রকাশের অন্তত বছর পাঁচেক আগেই, সিপাহী বিদ্রোহের দিনগুলিতে, ব্রিটিশবিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লক্ষ্মীবাঈ এবং তিনি এই পুরুষতান্ত্রিক রেজিমেন্টের সংস্কার বা ধারার মধ্যেই একটি প্রতিস্পর্ধী কাঠামোর কাহিনি বুনে দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।
এর অনেক আগেই আমরা পেয়েছি রানী দুর্গাবতীকে। পাশ্চাত্যের কাব্যের নারীচরিত্রগুলির মতই, ভারতীয় এই মেয়েরা বাস্তবের উদাহরণ হয়েই হয়তো প্রমীলা চরিত্রটির পরিকল্পনার অনুপ্রেরণা হয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে এদের সিদ্ধি বা সংগ্রাম, প্রমীলাকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যাননি মধুসূদন, হয়তো এতে তাঁর কাব্য-পরিকল্পনা ব্যাহত হতো বলেই।
পাশ্চাত্যের মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা মধুসূদনকে আকৃষ্ট করেছিল বরাবর। কখনও কখনও তাঁর নাটকের এবং কাব্যের মেয়েরা খানিকটা এমন স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়চেতা হয়ে উঠতে চেয়েছে। ভারতবর্ষে নারীমুক্তি ভাবনার একেবারে প্রথম পর্যায় তখন, অথচ পাশ্চাত্যে এর অনেক আগেই লিবারাল ফেমিনিজম বা উদারপন্থী নারীবাদের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ ও নারীর চিন্তা ও মেধার মধ্যে অসাম্য মুছে দিয়ে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের কথা ভাবা হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই সতীদাহ প্রথা রদ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আন্দোলন ইত্যাদি বহুবিধ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা শুরু হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য পরিচিত 'জেন্ডার বাইনারি'কেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর এই ধারণায় মেয়েরা সমাজ বা রাষ্ট্রে সবসময় দ্বিতীয় লিঙ্গ। পুরুষের কর্তৃত্বের স্বর কোনও-না-কোনওভাবে নারী-চরিত্রগুলির উপর চেপে বসেছেই। তবুও সেই ছকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কখনও কখনও নারীও পুরুষের কর্তৃত্বের বিরোধী স্বর আবিষ্কার করতে চেয়েছে। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে বিপর্যস্ত রাবণের কাছে পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা যখন পুত্রহত্যার কৈফিয়ৎ দাবি করে, অথবা রাবণকে এই দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে ভর্ৎসনা করে, তখন বারেকের জন্য মনে হয় যে, স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত এমন চরিত্র কাব্যের পুরুষ ছককে ভেঙে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে হয়তো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির কোন বিকাশই ঘটেনি কাব্যে। বরং ব্যক্তিত্বময়ী চিত্রাঙ্গদার প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনার স্বরকে সেখানে চাপা দেয় রাবণের রাজসত্তার অহমিকা। বীরবাহুর জন্য চিত্রাঙ্গদার শোকোচ্ছ্বাস দেখে যখন রাবণ সবিস্ময়ে বলে - "এক পুত্রশোকে তুমি ললনে/ শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে দিবানিশি", তখন এই শত পুত্রশোক এবং প্রজাবিয়োগের শোককে সহন করার মধ্যে রাবণের রাজসত্তার বিশালতা ধরা পড়ে, একথা সত্যি; কিন্তু নিজের সেই রাজসত্তাটিকে চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত মাতৃসত্তার সামনে প্রতিতুলনায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে, কোথাও যেন রাবণের পুরুষসত্তা নারীর (চিত্রাঙ্গদার) শোককে কিছু লঘু করে তুলতে চায় এবং এর দ্বারা নিজের পৌরুষকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায় রাবণ।
একান্ত ব্যক্তিগত আবেগের পরিসরেও পুরুষতন্ত্রের স্বর প্রাধান্য পেয়ে যায়। একারণেই মন্দোদরীর পাশে থেকে ব্যয় করার মতো সময় থাকে না রাবণের হাতে। পাছে মন্দোদরীর অশ্রুশোক ভুলিয়ে দেয় তার শত্রু-সংহারের কর্তব্য, একথা ভেবে দ্রুত তিনি মন্দোদরীর সঙ্গ ত্যাগ করে রণসজ্জায় সেজে ওঠার তাগিদ অনুভব করেন। রাবণের শোক এবং সামর্থ্য দুইয়েরই কোন তুলনা নেই, এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এমন কঠোর পুরুষ-মুদ্রায় রাবণকে সাজিয়ে তোলেন তিনি, যাঁর বুক-ভরা কান্না, অথচ কান্নার অবকাশ নেই। কোনও দৈবশক্তির কাছে সে প্রসাদপ্রার্থী নয়। একান্তেও বিলাপে পরাঙ্মুখ। কর্তব্যে নিরন্তর অবিচল। এই আগ্রাসী পৌরুষই হয়তো রাবণকে মহিমময় করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা একাও করে দিয়েছে। এই আগ্রাসী আক্রমণাত্মক পৌরুষের গভীরেই আছে আত্মধ্বংসের বীজ।
এই আগ্রাসী পুরুষতন্ত্রই সম্পদ এবং নারীর উপর তার একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে। অতএব সূর্পণখার অপমানের প্রতিবিধিৎসায় হোক, অথবা নিজের সম্ভোগবৃত্তির তাগিদেই হোক, সীতা-হরণের পর, অশোকবনে তাকে বন্দী করে রাখার মধ্যে পুরুষের যৌনতার আধিপত্যবাদই স্বীকৃতি পায়। এই স্পর্ধাশীল জিগীষু পৌরুষ, শার্দূল যেমন হরিণীকে, তেমনি সীতাকে অধিকার করেছে। নিত্য নারী-হরণ ও অসংযত ভোগবৃত্তি, রাবণের অজ্ঞাতে তার বিনাশের পথ প্রস্তুত করেছে। সমগ্র কাব্যে, মূলত রাবণকে কেন্দ্রে রেখে, পৌরুষের যে আখ্যান রচনা করা হলো, তার বিনাশের বীজ থেকে গেল নারী চরিত্রের মধ্যেই। চতুর্থ সর্গে, সরমার কাছে সীতা জানিয়েছে, তার স্বপ্নে দেখা, বসুন্ধরার মনোবাসনার কথা "তোর হেতু সবংশে মজিবে/ অধম। এ ভার আমি সহিতে না পারি,/ ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে।" নারীর দ্বারা পুরুষের এই শাস্তিবিধান ও ধ্বংসসাধন পুরুষের একচেটিয়া প্রাধান্যের মধ্যে একটি ভিন্ন কাহিনি রচনা করে। মধুসূদনের এই মহাকাব্যের স্বর্গ-মর্ত-পাতালজোড়া আখ্যানে, আমরা দেখেছি, ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছে লক্ষ্মী। রাবণ এবং মেঘনাদের বিনাশের পরিকল্পনা করতে বসে দেবী কাত্যায়নীর সহায়তা চেয়েছেন ইন্দ্র। পার্বতীকে অবশ্য রাবণের ধ্বংসের উপায় বলে দিলেন মহেশ্বর - "মায়ার প্রসাদে বধিবে লক্ষ্মণ শূর ইন্দ্রজিৎ শূরে।" কাজটি সহজ নয়, তবু মায়া প্রতিশ্রুতি দিলেন 'লঙ্কার পঙ্কজরবি যাবে অস্তাচলে'। সেই রাবণ-বধের যে আয়োজন করলো মায়া, তার বিবরণ কাব্যের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে আছে। নারী হরণের যে অন্যায় করেছিলেন রাবণ, মেঘনাদ হত্যার পরিকল্পনা করে, রাবণকে শোকের আঘাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে, যেন সেই অন্যায়ের শাস্তি দিল নারীশক্তিই। লক্ষ্মী কাত্যায়নী বা মায়ার মত সর্বত্র বিহারী, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মেয়েরা সেদিন বাংলাদেশে দুর্লভ বলেই হয়তো দেবলোক থেকে চরিত্রগুলিকে ধার করলেন কবি। এরা দেবলোকবাসিনী বলেই অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রমীলা নারী বলেই তার যুদ্ধ আহ্বান ফিরিয়ে দিয়েছিল রাম, অথচ ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে আড়াল থেকে কোন নীতির তোয়াক্কা না করে সংগ্রাম করল তো আসলে মায়াই। লক্ষ্মী, কাত্যায়নী, মায়া, এদের মিলিত ষড়যন্ত্রই শেষপর্যন্ত রাবণের পরাভব সম্ভব করে তুলল। নারীর ইচ্ছাশক্তি যে অসাধ্যকেও সম্ভব করে তুলতে পারে, তার স্পষ্ট ইশারা থেকে গেল এখানে।
তবে একে নারীর ক্ষমতায়ন বলে চিহ্নিত করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় থাকে। অলৌকিকতার জোর কখনও কখনও ইচ্ছাপূরণের কল্পনা জোগায় হয়তো, কিন্তু দেবলোকবাসিনীদের অলৌকিক ক্ষমতা এদেশের মেয়েদের কাছে সেদিন ক্ষমতার কোনও নতুন সূত্র এনে দেয়নি। আসলে ক্ষমতার যে বিশেষ সংগঠন তৈরী হয়ে আছে পুরুষতন্ত্রের মধ্যে, সেখানে পুরুষ সর্বত্রই নারীত্বের ধারণার নির্ণায়ক। পুরুষের এই আধিপত্যকামী দৃষ্টিভঙ্গিই যে কোনও অবস্থাতেই নারীকে সম্ভোগযোগ্য চেহারায় হাজির করতে চায়। তাই প্রমীলা যখন যুদ্ধসাজে সেজে উঠেছে, তখনও তার 'উচ্চকুচ', কটিদেশ, সুবর্তুল ঊরুর প্রতি হাইলাইট করেন মধুসূদন; দেবী কাত্যায়নী মোহিনীবেশেই মুগ্ধ করছেন শিবকে, নিজের শরীরের অর্ঘ্যেই মহেশ্বরের মনোরঞ্জন করতে হয়েছে তাকে, আবার এই পুরুষের উপনিবেশের মধ্যে বাস করেই প্রমীলা সহমরণে উদ্বুদ্ধ। প্রমীলার সপ্রতিভতা থেকে সহমরণ একদিকে, আর অন্যদিকে অশোকবনে সীতার অশ্রুমোচন এবং শ্রীরামসঙ্গ-স্মরণ - এই দুই-ই আসলে এ কাব্যে একমুখী একটি বয়ানই রচনা করেছে। পুরুষতন্ত্র দ্বারা নির্মিত, ভারতীয় নারীত্বের গ্রহণযোগ্য চিহ্নই মান্য করা হয়েছে এখানে। পুরুষের প্রভুত্ববাদ, সমাজ-নির্দিষ্ট কালচারাল কোডের মধ্যে এ কাব্যের নারীচরিত্রগুলিকে আটকে রেখেছে তো বটেই, কাব্যের মুখ্য পুরুষচরিত্রগুলিও এর ফলে আরও মহিমান্বিত হওয়ার সুযোগ হারিয়েছে।
চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।
